ভাষার উৎপত্তির সন্ধানে ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান, সাদিয়া শান্তা
‘ভাষা কেবল শব্দের সমাহার নয়। এটি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক, সম্প্রদায় সৃষ্টি ও একীভূতকরণের ইতিহাস। এ সবকিছুই একটি ভাষায় মূর্ত’ -নোম চমস্কি।
‘ভাষা একটি সংস্কৃতির মানচিত্র। ভাষা তোমাদের বলে দেবে একটি সংস্কৃতির মানুষ কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় যাচ্ছে’ -রিতা ব্রাউন।
উপরের দুটি উক্তি থেকেই বুঝা যায় কোন জাতির সংস্কৃতি বুঝতে হলে আগে তাদের ভাষা বুঝতে হবে। নৃ-গবেষকরা মাঠকর্মে গিয়ে কোন নির্দিষ্ট জাতির সংস্কৃতি বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভাষায় হস্তক্ষেপ করা ছাড়া কোন জাতির সংস্কৃতি অধ্যয়ন করা সম্ভব না। তাই নৃবিজ্ঞানের একটি প্রধান শাখা ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান। এই শাখায় কাজ করতে গিয়ে নৃতাত্ত্বিক এবং ভাষাতাত্ত্বিকদের মাথায় প্রথমেই যে চিন্তাটা আসে তা হলো ভাষার উৎস। তারা বুঝতে চায় ভাষার উৎপত্তি কবে হলো? কিভাবে হলো? ভাষার বিকাশ ঘটেছে কিভাবে? ভাষা মনোজেনেসিস নাকি পলিজেনেসিস? (ভাষাতত্ত্বে মনোজেনেসিস বলতে বুঝায় এমন ধারণা- একটি মাত্র ভাষা থেকে সকল ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে। অপরদিকে পলিজেনেসিস বলতে বুঝায় এমন ধারণা- প্রতিটি ভাষা আলাদা আলাদা উৎস থেকে উদ্ভূত ও বিকশিত হয়েছে।)
সক্রেটিসের সময়কাল থেকেই ভাষার উৎপত্তি সংক্রান্ত আলোচনাগুলি ছিল ভাষাতত্বিক এবং দার্শনিকদের প্রিয় আলাপ। প্লেটোর ‘ক্র্যাটাইলাস’ বইয়ে এমন একটি বিতার্কিক কথোপকথনের উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে দার্শনিক সোফিস্ট ক্র্যাটাইলাস দাবী করছেন জগতের সবকিছুর নামকরণের পেছনে রয়েছে একজন ‘নামকর্তা’র ভূমিকা। সেই নামকর্তা হতে পারে স্বয়ং ঈশ্বর কিংবা আদিমকালের কোন পৌরাণিক বীর৷ ক্র্যাটাইলাস মনে করেন নামকর্তা নামকরণ করে প্রতিটা জিনিসের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে। সক্রেটিস তখন ক্র্যাটাইলাসের দাবীর উপর কাউন্টার জারি করেন। তিনি প্রশ্ন তুলেন কিভাবে সেই নামকর্তা সবকিছুর নামকরণ করলো যদি তার পূর্বে কোন ভাষার অস্তিত্বই না থাকে যার মাধ্যমে নামকর্তা কোন জিনিসের অন্তর্নিহিত প্রকৃতিকে ভাষার মাধ্যমে চিহ্নিত করতে পারে? সক্রেটিসের এই প্রশ্নের মুখে খারিজ হয়ে যায় ক্র্যাটাইলাসের তত্ত্ব।
এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ডে ভাষার উৎপত্তি সংক্রান্ত আলোচনা আবার নতুন করে শুরু হয়। তারও কয়েক দশক পরে জার্মান মনোবিজ্ঞানী উইলহেম উন্ড লক্ষ্য করেন ভাষার উৎপত্তি নিয়ে যতো তত্ত্ব ও প্রস্তাবনা আলোচিত হয়েছে সবগুলোই দুটি বিপরীত দর্শন ইঙ্গিত করে- মানব জগতে ভাষার আবির্ভাব ও ব্যবহারের সক্ষমতা কোন ‘ঐশ্বরিক দান’ নাকি মানব জাতির বিবর্তনের সাথে সাথে এটি মনুষ্য জাতিরই উদ্ভাবন? এইসকল দর্শনকে ঘিরে উইলেম উন্ড ভাষার উৎপত্তি সংক্রান্ত চারটি প্রস্তাবনা উল্লেখ করেন। প্রস্তাবনাগুলোর পর্যায়ক্রমিক আলোচনার সাথে সাথে এখন আমরা যাব ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে কোন কোন মতবাদ কি প্রস্তাব করে, তা জানতে।

অলৌকিক তত্ত্ব (Miraculous Theory):
বাইবেল অনুযায়ী এই তত্ত্ব প্রস্তাব করে ভাষা একটি ‘Divine Gift’ বা স্বর্গীয় উপহার। সৃষ্টিকর্তা মানুষ সৃষ্টির শুরুতেই মানুষের মধ্যে শুধু ভাষাই নয় বরং কথা বলার ক্ষমতাও দিয়ে দিয়েছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ভাষার সাথে সম্পর্কিত ‘Tower of Babel’ এর পুরাণকাহিনীটিও ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের এই যুগে এসে উপযুক্ত যুক্তির অভাবে তত্ত্বটি শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি।
উদ্ভাবন তত্ত্ব (Invention Theory):
এই তত্ত্ব প্রস্তাব করে ভাষা হচ্ছে ‘human artifact’ অর্থাৎ মানুষের উদ্ভাবনী যা মানবমাজের চাহিদার প্রতিক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু এখানে মূখ্য সমস্যা দেখা দেয় ভাষা ও ভাষার অর্থের মধ্যে সম্পর্ক ও সমন্বয় ঘটানো নিয়ে। বিষয়টা একটু বিশ্লেষণ করে নিলে বুঝতে সুবিধা হবে।
ধরা যাক, আদিমকালে মানুষের সমাজে নানা প্রয়োজনে ভাষার ব্যবহার শুরু হয়। তখন তারা বিভিন্ন জিনিসের নাম দিতে থাকে যাতে সবাই একটি জিনিসকে একটি নির্দিষ্ট নামেই চেনে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোন জিনিসটার নামকরণ কি হবে তা কিভাবে নির্ধারিত হয়? যেমন ধরুন, বৃক্ষের নাম কেন বৃক্ষ হবে? মাছের নাম কেন মাছ হবে? প্রজাপতির নাম কেন প্রজাপতিই হবে? এই প্রশ্ন আবারো আমাদের ক্র্যাটাইলাসের দাবীর মুখে সক্রেটিসের কাউন্টার জারি করার সামনেই দাঁড় করায়। ঠিক এই জায়গাটাই এসেই ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুর প্রস্তাব করেন, ভাষা ও ভাষার অর্থের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি অনেকটা আর্বিট্রারি। সস্যুরের মতে, প্রকৃতি জগতে বিভিন্ন জিনিসের নামকরণ হয়েছিল আর্বিট্রারি অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী প্রক্রিয়ায়। আর্ব্রিট্রারিনেস বুঝাতে গিয়ে সস্যুর নিয়ে আসেন তার স্ট্রাকচারাল থিওরি বা কাঠামোতত্ত্ব। কাঠামোতত্ত্বে উঠে আসে Signifier (চিহ্নকারী) ও Signified (চিহ্ন) এর সম্পর্ক। কোন জিনিসকে যে নামে ডাকা হয় বা যে প্রতীকের মাধ্যমে নির্দেশ করা হয় তা হলো সিগনিফায়ার এবং খোদ সেই জিনিসটি হলো সিগনিফাইড। সস্যুরের মতে, সিগনিফায়ারের প্রকৃতি স্বেচ্ছাচারী। অর্থাৎ সিগনিফায়ার ও সিগনিফাইডের সংযুক্তিতে কোন অনিবার্যতা নেই। আর এ কারণেই স্থানভেদে, কখনো বা কালভেদে ভাষার অর্থ বদলায়।
অনুকরণ তত্ত্ব (Imitation Theory / onomatopoeia):
এটি ‘Bow-Wow’ থিওরি নামে অধিক পরিচিত। এই থিওরি মতে, ভাষার ব্যবহার শুরু হয়ে আদিম প্রকৃতির বিভিন্ন ধ্বনির অনুকরণে। ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী জন লুবক এই থিওরির একজন প্রবক্তা। জন লুবকের মতে অনেক প্রাণীরই নামকরণ হয়েছে তাদের উচ্চারিত ধ্বনির সাথে সামঞ্জস্য রেখে। যেমন- কাক, কোকিল ইত্যাদি৷ এছাড়াও ‘bang’, ‘crack’, ‘whizz’, ‘hum’ ইত্যাদি শব্দ এসেছে উদ্ভুত পরিস্থিতির সাপেক্ষে।
যেমন ধরা যাক, আদিম কালে একদল মানুষ শিকারে গেল। তাদের মধ্যে কেউ একজন কোন একটা জায়গায় একটি ‘শিকার’ দেখতে পেল। এখন সে তার দলের বাকি শিকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য এবং কোন শিকার আছে তা বুঝাবার জন্য সেই শিকারের ধ্বনির মতো ধ্বনি করলো। তাতে করে দলের সবাই বুঝতে পারল কোন শিকার তাদের সামনে আছে। এভাবেই বিভিন্ন ধ্বনি সৃষ্টির মাধ্যমে তারা আস্তে আস্তে ভাষা ব্যবহারের দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু এই তত্ত্বটিও ভাষার উৎসের সন্ধানে পরিপূর্ণতা যোগান দিতে ব্যর্থ হয়। কেননা উদ্ভাবন তত্ত্বের আর্বিট্রারি প্রক্রিয়ায় যেসব শব্দের আলাপ উঠে আসে, সেসব শব্দের উৎস বিশ্লেষণে অনুকরণ তত্ত্ব খুব একটা জুতসই হাতিয়ার নয়। তাই এই তত্ত্বকে পূর্ণতা দিতে চলে আসে নতুন আরেকটি তত্ত্ব- প্রাকৃতিক ধ্বনি তত্ত্ব।
প্রাকৃতিক ধ্বনি তত্ত্ব (Natural Sound Theory):
এই তত্ত্ব মতে ভাষা উদ্ভূত হয়েছে মানুষের সহজাত আচরণ থেকে। এর সাথে যুক্ত রয়েছে বিবর্তনবাদ তত্ত্ব, উনবিংশ শতাব্দীতে এসে চার্লস ডারউইন যে তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রাকৃতিক ধ্বনি তত্ত্ব বিবর্তনবাদের সাথে যুক্ত হয়ে প্রস্তাব করে, মানুষ প্রথমে তার সহজাত আচরণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধ্বনি ব্যবহার করতে শেখে। যেমন- কান্নাকাটির সময় একধরনের ধ্বনি তৈরী হয়, হাসির সময় এক ধরনের ধ্বনি তৈরী হয়, আবার ব্যথা পেলেও আমাদের মুখ থেকে এক ধরনের ধ্বনি তৈরী হয়। এই সমস্ত ধ্বনি বা আওয়াজ পরবর্তীতে মানুষের বিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ভাষা ব্যবহারে সক্ষমতা এনে দেয়। বিবর্তনের ফলে বানর বা এইপ (Ape) জাতীয় অন্যান্য প্রাণীর সাথে মানুষের মধ্যে অনেক জৈবিক পার্থক্য তৈরী হয়েছে। যার ফলে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় মানুষ কথা বলতে সক্ষম হলেও অন্যান্য প্রাণী কথা বলতে পারে না। যেমন- মানুষের শরীরে এফওএক্সপিটু (FOXP2) জিনটি রূপান্তরিত অবস্থায় আছে। এই জিনটি কেবল রূপান্তরিত অবস্থায় থাকলেই তা প্রাণীর কথা বলার পক্ষে সহায়ক। কিন্তু শিম্পাঞ্জীর মধ্যে এটি রূপান্তরিত অবস্থায় থাকে না। ফলে বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ কথা বলতে পারলেও শিম্পাঞ্জী কথা বলতে পারে না।
ভাষার উৎপত্তির সময়কালঃ
একটা সময় ধারণা করা হতো পঞ্চাশ হাজার বছর আগে ভাষার ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে ভাষাতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃবিজ্ঞানীদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় এখন জানা যায় প্রায় চার লক্ষ বছর আগে নিয়ান্ডারথালদের সময়কালে ভাষার ব্যবহার শুরু হয়। নিয়ান্ডারথালদের জৈবিক কাঠামো, শ্বসনতন্ত্র, কণ্ঠের অবস্থা ইত্যাদি কথা বলার জন্য উপযোগী ছিল৷ বক্ষ ও উদরের মাঝখানের ঝিল্লিতে নার্ভের সংখ্যা বেশি হলে এবং স্পাইনাল কর্ড মোটা হলে তা কথা বলার পক্ষে সহায়ক। মানুষের মতো নিয়ান্ডারথালদের ঝিল্লিতেও নার্ভের সংখ্যা বেশি ছিল এবং স্পাইনাল কর্ড মোটা ছিল। এছাড়াও নিয়ান্ডারথালদের দেহে ‘এফওএক্সপিটু’ (FOXP2) নামক জিন’টিও রূপান্তরিত অবস্থায় ছিল যা ভাষা ব্যবহারে সহায়ক। অর্থাৎ নিয়ান্ডারথালরা মানুষের মতো ভাষা ব্যবহারে সক্ষম ছিল তখনই ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল।
ভাষার উৎপত্তির আলাপ ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানে এখনো এক আলোচিত অধ্যায়। উইলহেম উন্ডের প্রস্তাবনার বাইরেও ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশের রয়েছে আরো অনেক ধারা। নৃবিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন ভাষার মানচিত্র (Language Maps) যার সূত্র ধরে তারা বুঝতে চান কেন পৃথিবীর তাবৎ ভাষার এত বৈচিত্র্য! ভাষার বৈচিত্র্য ঘটার পর আজকের বর্তমান সময়ে আবার শুরু হয়েছে ভাষার বিলুপ্তির আলোচনা। শুধুমাত্র ভাষাতাত্ত্বিকের পক্ষে সম্ভব নয় অঞ্চলভেদে, জাতিভেদে ভাষার সম্পর্ক নির্ণয় করা, ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশের ধারা নিশ্চিত করা কিংবা ভাষা বিলুপ্তির কারণ চিহ্নিত করা। তাই ভাষাতত্ত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ভাষা সমস্যার সমাধানে কাজ করে আসছে নৃবিজ্ঞান- তথা ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান।
Reference
Linguistic Anthropology – Nancy Parrott Hickerson (second edition)

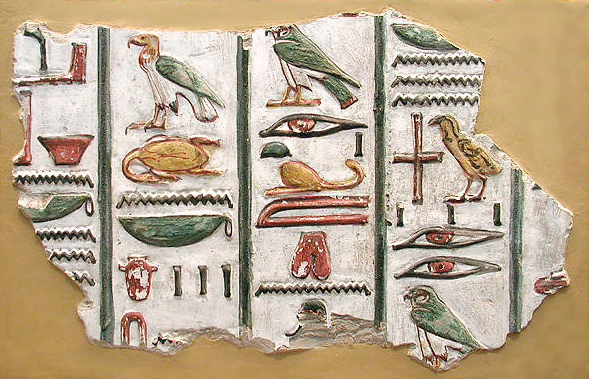
খুব সুন্দর হয়েছে। আসলে, মাতৃভাষায় জ্ঞান অর্জনের মজাই আলাদা। ধন্যবাদ সাদিয়া শান্তা।